বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রচনার একটি নমুনা তৈরি করে দেয়া হল। আশা করি এটি শিক্ষার্থীদের কাজে লাগবে। তবে আমরা রচনা মুখস্থ করা নিরুৎসাহ দেই। আমরা নমুনা তৈরি করে দিচ্ছি একটা ধরনা দেবার জন্য। এখান থেকে ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীদের নিজের মতো করে নিজের ভাষায় রচনা লিখতে হবে।
Table of Contents
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যত বেশি সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাও তত বেশি। দেশের শ্রম, মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে।
প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার দেশের দ্রুত শিল্পায়নে সহায়তা করে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে। বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, মূলধন এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।
ফলে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এজন্য যথার্থই বলা হয়, ‘Bangladesh is a rich country inhabited by poor people : বস্তুত প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাবে বাংলাদেশ আজও অনুন্নত রয়ে গেছে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।
প্রাকৃতিক সম্পদ
‘প্রাকৃতিক সম্পদ’ বলতে প্রকৃতি-প্রদত্ত সকল সম্পদকে বুঝায়। প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির অবাধ দান যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা, নদ-নদী, কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, শক্তি সম্পদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।
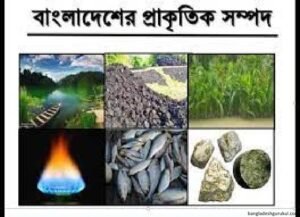
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ
দেশে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃতি ও বিন্যাস ভিন্নতর। প্রাকৃতিক সম্পদের উপকরণসমূহ দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা তথা সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো:
বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ
প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। প্রয়োজনের তুলনায় এ দেশে খনিজ সম্পদের পরিমাণ খুবই কম। ফলে প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ খনিজ সম্পদই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশে যে সকল খনিজ সম্পদ রয়েছে তার বর্ণনা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হলোঃ
১. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক কয়লা
কয়লা হলো শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি অঙ্গারময় পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত সহজে দাহ্য এক শ্রেণীর শিলাবিশেষ, যা উদ্ভিদজাত পদার্থ থেকে ভূ-গর্ভের চাপ ও তাপের সাহায্যে দৃঢ়ীকরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। কয়লা শক্তির অন্যতম উৎস। কয়লা দ্বারা কল-কারখানা, জাহাজ, রেলগাড়ি মোটরগাড়ি প্রভৃতি পরিচালিত হয় । তাছাড়া কালা জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলাদেশ কলো সম্পদে তত উন্নত নয়।
বাংলাদেশে যে কালো পাওয়া যায় তার অধিকাংশই নিকৃষ্টমানের। এ দেশের ফরিদপুরে বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলা বিল এবং সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে ৷ এছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্টমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।
১৯৮৫ সালে দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া এলাকায় বিরাট কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার অসুবিধার কারণে সকল খনি থেকে কয়লা উত্তোলন সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমাণ কয়লা মজুদ আছে তা উত্তোলন করতে পারলে প্রায় ২ শত বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

২. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক খনিজ তেল
পেট্রোলিয়ামের তরল অবস্থান হলো খনিজ তেল, যা ভারি হাইড্রো-কার্বন যৌগসমূহের সমষ্টি। খনিজ তেল অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা বাংলাদেশে প্রচুর খনিজ তেল পাওয়া যাবে। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান কার্য চালানো হচ্ছে। কিন্তু খনিজ তেল সম্পদের আবিষ্কার ও উত্তোলনে মোটেই অগ্রগতি হয়নি।
তবে ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই খনিজ তেল পাওয়া যায়। ২০২০ থেকে ২০৩০ মিটার গভীরতায় প্রায় ১০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল এখানে মজুদ আছে। তবে উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় প্রায় ৬ মিলিয়ন ব্যারেল। ১৯৮৭ সাল থেকে বেশ কয়েক বছর প্রতিদিন প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ ব্যারেল তেল উৎপাদন করা হলেও পরবর্তীতে তা কমে আসে।
একটি বিতর্কিত তেল কোম্পানির হাতে কূপটি অর্পণ করায় যথার্থ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দেয়। ফলে ১৯৯৪ সালের জুলাই মাস থেকে তেল উত্তোলন স্থগিত রয়েছে। সিলেটের হরিপুর ছাড়াও ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ ও কৈলাসটিলা-২ রূপে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু কারিগরি জটিলতার কারণে তেল আধারের ব্যাপ্তি ও তেলের পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।
৩. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক চুনাপাথর
চুনাপাথর এক জাতীয় পাললিক শিলা। এর প্রধান উপাদান হলো ক্যালসাইট। ক্যালসাইট ছাড়াও সামান্য ডলোমাইট কাঁদামাটি ও সিলিকা থাকতে পারে। চুন তৈরির ক্ষেত্রে চুনাপাথর বহুপ্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সিমেন্ট তৈরির মূল উপাদান এই চুনাপাথর।
এছাড়া লৌহ, কাগজ, গ্লাস, ব্লিচিং পাউডার, সাবান প্রভৃতি শিল্পে চুনাপাথরের ব্যবহার হয়ে থাকে। বাংলাদেশ চুনাপাথর সম্পদে সমৃদ্ধ নয় । সিলেট জেলার জাফলং, জকিগঞ্জ; সুনামগঞ্জ জেলার ভান্ডারঘাট, বাগালিবাজার, লালঘাট ও টাকেরঘাট এবং চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড ও কক্সবাজার জেলার সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপে চুনাপাথর পাওয়া যায়। এছাড়া রাজশাহী বিভাগে জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ ও জয়পুরহাটে চুনাপাথর পাওয়া যায়।

৪. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক চীনামাটি :
বাংলাদেশের নেত্রকোনার বিজয়পুর এবং রাজশাহী জেলার পত্নীতলায় চীনামাটি পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুর গ্রামে প্রায় ২৬ কিমি দীর্ঘ এবং কয়েক মিটার প্রস্থ এলাকা জুড়ে প্রধান খনি অবস্থিত। এ খনিতে সঞ্চিত চীনামাটির পরিমাণ আনুমানিক ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টন।
বাংলাদেশের মোট চাহিদার প্রায় ৫০ ভাগ চীনামাটি এ খনি হতে উত্তোলন করা হয় । পত্নীতলার চীনামাটি খনিটি ৪১১ মিটার মাটির নিচে এবং স্তরটি প্রায় ৯ মিটার পুরু। চীনামাটি প্রধানত বাসনপত্র, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর, স্যানিটারি সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, কৃত্রিম বস্ত্র ও বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক শিল্পেও চীনামাটি ব্যবহৃত হয়।
৫. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক তামা :
বাংলাদেশের রংপুর জেলার রাণীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সঙ্গে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব খনি হতে তামা উত্তোলনের জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র, মুদ্রা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে তামার প্রয়োজন হয় ।
৬. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সিলিকা বালু :
প্রধানত কাচ নির্মাণে সিলিকা বালু ব্যবহৃত হয়। এছাড়া রাসায়নিক দ্রব্য, রঙ, অগ্নিরোধক ইট ইত্যাদি তৈরিতে সিলিকা বালু ব্যবহার করা হয়। সিলেটের নয়াপাড়া, ছাতিয়ানি, শাহজীবাজার ও কুলাউড়া চট্টগ্রামের দোহাজারী, জামালপুরের গারো পাহাড়ের বালিঝুরি এবং কুমিল্লা জেলার কালিকাপুর মৌজায় সিলিকা বালু পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট সিলিকা বালু উৎপাদিত হয়।

৭. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক পারমাণবিক খনিজ পদার্থ :
পারমাণবিক খনিজ পদার্থ (Atomic minerals) সাধারণত ভারী ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর খনিজ বালির সন্ধান পাওয়া গেছে। পারমাণবিক খনিজ পদার্থগুলো হলো জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, লিউকরেন প্রভৃতি।
৮. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গন্ধক
বারুদ, কীটপতঙ্গ নাশক ওষুধ তৈরি, এসিড, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, নিয়াশলাই, আতশবাজি প্রভৃতি তৈরিতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়া যায় ।
৯. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক নুড়ি পাথর
সিলেট জেলার লুবা, ভোলাগঞ্জ ও জিয়নগঞ্জ; দিনাজপুর জেলার পঞ্চগড় এবং লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রচুর নুড়ি পাথর পাওয়া যায়। প্রধানত রাস্তাঘাট, গৃহ, পুল, কালভার্ট, রেল লাইন প্রভৃতি নির্মাণে নুড়ি পাথর ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি নুড়ি পাথর পাওয়া যায় সিলেটে।
১০. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক খনিজ বালি :
চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর Radio Active Sand পাওয়া গেছে। এর মোট পরিমাণ ৫ লক্ষ টন বলে অনুমান করা হয়। এতে প্রচুর ভারি খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকায় এটি ভারী ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
১১. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক লবণ
খনিজ সম্পদ হিসেবে লবণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে কোনো লবণের খনি না থাকলেও সমুদ্রের লোনা পানি আটকিয়ে কুটির শিল্পের ভিত্তিতে উপকূলীয় জেলাগুলোতে প্রচুর লবণ উৎপাদন করা হয়। সরকারের অর্থানুকূল্যে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বছরে প্রায় ২ কোটি মণ লবণ উৎপাদন করা হয় ৷
লবণ উৎপাদন শিল্পে প্রায় ৫০-৬০ হাজার লোক নিয়োজিত রয়েছে। লবণ প্রধানত খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া চামড়া পরিশোধন, রাসায়নিক শিল্প, কষ্টিকসোডা প্রস্তুত এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে লবণ ব্যবহৃত হয় । বাংলাদেশে লবণ উৎপাদন অনেকটা প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। ফলে কোনো বছর লবণ উৎপাদন উদ্বৃত্ত হয়, আবার কোনো বছর লবণ বিদেশ হতে আমদানি করতে হয় ।

১২. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক কঠিন শিলা :
কঠিন শিলা বলতে মূলত আগ্নেয় শিলাকে বুঝায়। পৃথিবী সৃষ্টির সময় উত্তপ্ত গলিত তরল ম্যাগমা জাতীয় পদার্থ ক্রমান্বয়ে শীতল ও কঠিন হয়ে যে কেলাসিত শিলার সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয় শিলা বলা হয়। এই শিলা খুবই শক্ত বলে গৃহ, সড়ক, বাঁধ, রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণ কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।
রংপুর জেলার রানীপুকুর ও শ্যামপুরে এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। রংপুরের রানীপুকুর থেকে বৈদেশিক সহযোগিতায় শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এখান থেকে বছরে প্রায় ১৭ লক্ষ টন শিলা উত্তোলন করা যাবে ।
অন্যদিকে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প ২০০৪-২০০৫ সালে সমাপ্ত হবে, যা থেকে প্রতি বছর প্রায় ১.৬৫ মিলিয়ন টন কঠিন শিলা উত্তোলন করা সম্ভব হবে।
১৩. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস :
সর্বাপেক্ষা সহজ ও হালকা হাইড্রো-কার্বন মিথেন (CH4) গ্যাস দিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস গঠিত । প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। ১৯১০ সাল থেকে এ দেশে অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে সিলেটে সর্বপ্রথম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়।
দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার উৎপাদন, বাণিজ্যিক, শিল্প ও গৃহস্থলী খাতে জ্বালানির অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ জ্বালানি সম্পদ সমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রধানতম উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস।
এই গ্যাস দেশের মোট জ্বালানি চাহিদার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ পূরণ করে। এ যাবত দেশে আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২২টি। এই ২২টি গ্যাস ক্ষেত্রে মোট প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৮.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ২০.৫১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।
বর্তমানে ১৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৫৫টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এই ১৫টি গ্যাস ক্ষেত্র হচ্ছে তিতাস (১৪টি কূপ), বাখরাবাদ (৪টি কূপ), হবিগঞ্জ (৯টি কূপ), রশিদপুর (৭টি কূপ), কৈলাশটিলা (৩টি কূপ), সিলেট (১টি কূপ), মেঘনা (১টি কূপ), সালদানদী (২টি কূপ), সাঙ্গু (৩টি কূপ), জালালাবাদ (৪টি কূপ), বিয়ানীবাজার (২টি কূপ), ফেঞ্চুগঞ্জ (২টি কূপ) এবং ফেণী (২টি কূপ)।
ছাতক ও ফেনী গ্যাসক্ষেত্র দুটি দীর্ঘদিন উৎপাদনশীল থাকার পর বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। মোট উৎপাদিত গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৪৩%, সার উৎপাদনে ৩৪%, শিল্প ও কলকারখানায় ২৬%, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ২% এবং গৃহস্থালীতে ৫% গ্যাস ব্যবহৃত হয় । বর্তমানে দেশে উৎপাদিত প্রায় ৯০% বিদ্যুৎ তৈরি হয় গ্যাস নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰসমূহে ।
প্রাকৃতিক গ্যাস অফুরন্ত নয় । তাই নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্যাস সম্পদের দ্রুত অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারা দেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সুবিধাজনক শর্তে উৎপাদন বণ্টন চুক্তির আওতায় বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীর পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে।
প্রথম ও দ্বিতীয় পিএসসি (Production Sharing Contract) বিডিং-এর আওতায় এ পর্যন্ত ১২টি ব্লকের জন্য উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল কোম্পানির মধ্যে ১টি কোম্পানি বঙ্গোপসাগরে একটি গ্যাস ক্ষেত্র (সাঙ্গু) আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে এবং ১৯৯৮ সাল থেকে পিএসসি ব্যবস্থার অধীনে সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উৎপাদন শুরু হয়েছে। আরো একটি কোম্পানি নতুন দু’টি স্থানে (বিবিয়ানা ও মৌলভীবাজার) গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে ।

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ
মৎস্য বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি, বিল ও হাওর রয়েছে। এ সকল জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলভাগের লোনা পানিতেও প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। প্রাপ্তিস্থানের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদকে দু’ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ক. সামুদ্রিক মৎস্য; খ. মিঠা পানির মৎস্য:
ক. বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য :
বাংলাদেশ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সীমান্ত রেখা হতে টেকনাফ পর্যন্ত ৭২০ কি: মি: তটরেখাসহ নিজস্ব জলসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা আমাদের সামুদ্রিক বিচরণ ক্ষেত্র। বাংলাদেশের জলসীমার দ্বীপসমূহের মধ্যে সেন্টমার্টিন উপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, দুবলার চর, বড় বাইশদিয়া প্রভৃতি স্থান মৎস্য শিকার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। এখানে মৃত তমসার মধ্যে ভেটকি, রূপচাঁদা, লাক্ষা, চুরি, কোরাল, গলদা চিংড়ি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
খ. বাংলাদেশে মিঠা পানির মৎস্য
বাংলাদেশের প্রায় ৭,২৪০ কিমি দীর্ঘ নদী, অসংখ্য খাল-বিল, পুকুর, হাওর-বাওর এবং বর্ষাকালীন বিস্তৃত প্লাবিত এলাকা মিঠা পানির মৎস্যের বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে পরিগনিত। এসব স্থানে প্রাপ্ত মৎস্যের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, শোল, বোয়াল, গজার, পাঙ্গাস, আড় কালবাউস, কৈ, শিং, মারে, চিংড়ি, টেংরা, সরপুটি, টাকি, তেলাপিয়া, পাবদা, তপসী প্রভৃতি মাছ উল্লেখযোগ্য।

মৎস্য সম্পদের গুরুত্ত্ব ও বর্তমান অবস্থা
মৎস্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচিত। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্যখাতের অবদান উল্লেখযোগ্য।
এ সেক্টরের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে প্রায় ১২ লক্ষ এবং খণ্ডকালীন ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ সম্পৃক্ত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৪.৪ লাখ হেক্টর। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪০.৪৭ লাখ হেক্টর যা মোট জলাশয়ের প্রায় ৯১.১%। বাকি ৮.৯% বন্ধ জলাশয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ২১.০২ লাখ মেট্রিক টন।
এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বন্ধ জলাশয় ও সামুদ্রিক জলাশয় হতে যথাক্রমে ৭.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন, ৯.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৪.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণীজ আমিষের প্রায় ৬৩ শতাংশ আসে মাছ থেকে।
বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু মাছ সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ২৮ গ্রাম, যেখানে প্রয়োজন কমপক্ষে ৩৫ গ্রাম জাতীয় আয়ের ৫.৩% এবং দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬% আসে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি থেকে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৫৪.১৪১ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২৩৬৩.৪৭ কোটি টাকা আয় হয়েছে।
বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষের উন্নত প্রযুক্তি বেসরকারি পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলে দীঘি-পুকুর তথা বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। মূলত দেশে এখন ব্যক্তি মালিকানাধীন খামার ও হ্যাচারি দিন দিন। বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে মাছের উৎপাদন যেমন বাড়ছে, তেমনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে।
পাশাপাশি বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ছে। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি জলাশয় সংস্কার ও উন্নয়ন হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকায় সমন্বিত মৎস্য চাষ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ, হ্যাচারি স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চিংড়ি আহরণের পর চিংড়ির গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০টি চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী সরকারি পর্যায়ে ১১২ টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৬৯৬টি সহ দেশে সর্বমোট ৮০৮টি মৎস্য হ্যাচারি ও খামার রয়েছে । এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ১৭০০টি মৎস্য খামার আছে।

বাংলাদেশের পশুসম্পদ
পশু সম্পদ বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের পশুসম্পদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) বন্য প্রাণী, (২) গৃহপালিত পশু। দেশের বনাঞ্চলে যে সকল প্রাণী বাস করে সেগুলো বন্য প্রাণী।
এ সকল বন্য প্রাণীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো হাতি, বাঘ হরিণ, চিতাবাদ, শুকর, বনবিড়াল, শিয়াল, বানর, সরীসৃপ এবং নানা ধরনের পাখি, পক্ষান্তরে, গৃহস্থদের বাড়িতে যে সকল প্রাণী পালন করা হয় সেগুলো গৃহপালিত পশু নামে পরিচিত। সাধারণভাবে পশুসম্পদ বলতে গৃহে পালিত বিভিন্ন প্রকার পশু ও পাখিকে বোঝায়। বাংলাদেশ পশুসম্পদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়।
কারণ, বাংলাদেশের জলবায়ু যদিও শতপালনের উপযোগী, কিন্তু পশুচারণ ক্ষেত্রের অভাবে বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পশুপালন করা হয় না। তবে দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক পরিবারই নিজ নিজ প্রয়োজনে কম-বেশি পশু-পাখি পালন করে থাকে।
এ সব গৃহপালিত পশু সম্পদের মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, ঘোড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল পশু পালন করে যে সকল পশুজাত দ্রব্য বা প্রাণিজ সম্পদ পাওয়া যায় তার মধ্যে মাংস, ডিম, দুধ, দুগ্ধজাত দ্র্য, চামড়া, প্রাণিজ্য চর্বি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় অর্থনীতিতে পশুসম্পদের গুরুত্ব
একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পশুসম্পদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ । খাদ্য ঘাটতি হ্রাস, সুগম খাদ্য সরবরাহ, কৃষি কাজ পরিচালনা, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পের কাচামাল সরবরাহ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরসস্থান কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। আর এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে পশুসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গতসম্পদ খাত বর্তমানে অন্যতম যুৎসই মাধ্যম হিসেবে বিচিত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুজাত দ্রব্য, যেমন- চামড়া, পালক, পশম ও হাড় ইত্যাদির ভূমিকা যোগ।
২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) পশুসম্পদ খাতের অবদান ২.১% এবং কৃষি খাতে এর অবদান ১৬.১৯%। যান্ত্রিক চাষাবাদের পাশাপাশি দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ ভূমিকর্ষণ বলদের সাহায্যে করা হয়ে থাকে। দেশে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ জনগোষ্ঠী সরাসরি ও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আংশিকভাবে পশুসম্পদের ওপর নির্ভরশীল।
বেসরকারিখাত ও এনজিওসমূহ সংশ্লিষ্টকরণের ফলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ খাতের ভূমিকা প্রশংসনীয় পশুসম্পদ অধিদপ্তরের এক তথ্যে দেখা যায়, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে গত বছর পর্যন্ত বেসরকারি মালিকানায় ছোটবড় প্রায় ৩৫ হাজার দুগ্ধ খামার ও ১ লক্ষ ২৯ হাজার হাঁস-মুরগির খামার গড়ে উঠেছে।
পশুসম্পদের বর্তমান অবস্থা
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪ ১৯ কোটি এবং ১১.০৫ কোটি। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.৪৪ কোটি ও ২২ কোটি। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে হাঁস-মুরগির মোট ডিমের উৎপাদন ছিল ৩৭৯ কোটি।
২০০৪-০৫ অর্থবছরে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫১৬ কোটি। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে দুধ এবং মাংসের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৩.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ৪.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে দুধ ও মাংসের উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০.৩ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৯.৬ লক্ষ মেট্রিক টন।
পশুসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম
দেশে পশুসম্পদের ব্যাপক ঘাটতির কারণ হিসেবে রোগ- ব্যাধি, নিম্নজাতের পশু, পশু খাদ্য ও গোচারণ ভূমির প্রকট অভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। সরকার বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করে এ সকল অসুবিধা দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশে পত চিকিৎসকের অভাব নিরসনকল্পে সরকার ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও দিনাজপুরে চারটি ভেটেরিনারী কলেজ চালু করেছে।
পশুসম্পদের উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে ব্যাপক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করা হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প, পোল্ট্রি সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প, পশুপাখির রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা উৎপাদন প্রকল্প, জাতীয় পশুসম্পদ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প অংশীদারিত্বমূলক পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ সরকার বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশের বনজসম্পদ
যে সকল ভূমিতে ছোট, মাঝারি বা বড় ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের বৃক্ষের সমাবেশ ঘটে তাকে বনভূমি বলে। আর বনভূমিতে উৎপাদিত বা প্রাপ্ত সম্পদকে বনজ সম্পদ বলা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বন আমাদের জীবন ও প্রকৃতির এক অমূল্য সম্পদ।
বন ছাড়া এ পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ তথা খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তাসহ এ পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পিছনে বনজসম্পদের অবদান সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার।
একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পরিবেশ রক্ষার জন্য সে দেশের মোট আয়তনের ২৫% বনভূমি থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২৫ লক্ষ হেক্টর যা বাংলাদশের মোট ভূ-খণ্ডের প্রায় ১৭%।
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং আরো কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসাব মতে, বর্তমানে এ দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ মোট আয়তনের ১০ শতাংশেরও কম। তাছাড়া মোট বনাঞ্চলের মধ্যে মাত্র ৪৫% এলাকায় গাছপালা রয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের বনজসম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য এবং জ্বালানি সংকট দূর করার জন্য বনাঞ্চলের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে।
বাংলাদেশের বনজসম্পদের বিবরণ
বৃক্ষের জন্ম ও বৃদ্ধি নির্ভর করে জলবায়ু ও মৃত্তিকার ওপর। জলবায়ুর তারতম্য ও মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতির পার্থকাহের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বৃক্ষ বা উি জন্মে। জলবায়ু, মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এদেশের বনভূমিকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় । যথা ১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্র-পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি, ২. ক্রান্তীয় পত্র-পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন, ৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন ।

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্র-পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি
অবস্থান ও আয়তন :
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভাগের জেলাগুলোর পাহাড়িয়া এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এ বনভূমি গড়ে উঠেছে। এ বনভূমির আয়তন প্রায় ১২ হাজার ৪১০ বর্গ কিমি। এর মধ্যে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ২ হাজার ১০০ বর্গ কিমি, রাঙামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলায় ৯ হাজার ৩০৭ বর্গ কিমি এবং সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় ১ হাজার ৩ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে এ বনাঞ্চল গঠিত। এর মধ্যে রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে মোট বনভূমির ৭৫ ভাগের অধিক অবস্থিত। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চল বাংলাদেশের মোট বনভূমির প্রায় ৬৫ ভাগ ।
গড়ে ওঠার কারণ :
পাহাড়ি মৃত্তিকা, প্রয়োজনীয় অত্যাধিক তাপমাত্রা (৩৪ সে) ও বৃষ্টিপাত (৩০০ সে মি), স্বল্প জনবসতি, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মানুষের বৈষয়িক কার্যাবলী কম হওয়ায় এ এলাকায় নিরক্ষীয় বনাঞ্চলের মতো চিরহরিৎ গভীর অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে।
বনজ সম্পদসমূহ :
উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুন এ অঞ্চলে বনভূমি গড়ে উঠেছে। চিরহরিৎ বৃক্ষের মধ্যে ময়না, তেলসুর, চাপালিস প্রভৃতি প্রধান । পর্ণমোচী বৃক্ষের মধ্যে গর্জন, গামারি, জারুল, সেগুন, কড়াই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
এছাড়াও এ বনাঞ্চলে নারিকেল, জলপাই, চাম্পা, টুন, তালি, চিকরাশি, মৌল, তাপাতি, কাঞ্চন, সাজনা, সিধা, কদম, বড়মালা, ছাতিয়ানি, টোনা, সোনালু, পিটালী, বাদাম, ডাইলা, ডুমুর, আমলকি, জাম, রিটা, বহেরা, রক্তন, বাটনা, কনক, থালি, হরিনা প্রভৃতি গাছ প্রচুর জন্যে । এছাড়া বাঁশ, বেত হোগলা, ঘাস, মুরতা, মোম, মধু, বন্যজন্তু, শিং, চামড়া, দাঁত, ওষুধি গাছপালা, রাবার এবং অন্যান্য প্রচুর বনজ সম্পদ এ বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়।
২. ক্রান্তীয় পত্র-পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন :
ক্রান্তীয় অঞ্চলে যেসব গাছের পাতা বছরে একবার সম্পূর্ণ ঝরে যায় সেগুলোকে ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছ বলা হয়। বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহে এ বনভূমি রয়েছে। পর্যাপ্ত তাপমাত্রা ও পরিমিত বৃষ্টিপাতের অভাবে শীতকালে এ বনাঞ্চলের গাছের পাতা ঝরে যায়। বাংলাদেশের এ বনভূমি দু’টি অংশে বিভক্ত। যথা- (ক) মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি, (খ) ঠাকুরগাঁও, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বনভূমি । নিচে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো

ক. মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি :
ময়মনসিংহ জেলার প্রায় ২০৮ বর্গ কিমি, টাঙ্গাইল জেলার প্রায় ৪১২ বর্গ কিমি এবং গাজীপুর জেলার প্রায় ৩৩৫ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে এ বনাঞ্চল অবস্থিত। এটি ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় মধুপুর গড় এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় নামে পরিচিত।
এ বনাঞ্চলে প্রচুর গজারি বৃক্ষ জনে বলে একে গজারি বৃক্ষের বনভূমিও বলা হয়। এ অরণ্যের অন্যান্য বৃক্ষগুলোর মধ্যে কড়ই, হিজল, বহেরা, হাড়গজা, হরিতকী, কাঁঠাল, নিম ইত্যাদি প্রধান। গজারি বৃক্ষ প্রায় ১৫ হতে ২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এটি জ্বালানি কাঠ, বাড়িঘর নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ বনাঞ্চলে কিছু কিছু ঘাস ও শন জনে। শন ঘর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
খ. ঠাকুরগাও, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বনভূমি
বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমিতে এ বনভূমি দেখা যায়। এর আয়তন প্রায় ২২ বর্গ কিলোমিটার। ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমির মত এ বনভূমির প্রধান বৃক্ষ শাল ও গজারি। এজন্য একে ভাওয়াল ও মধুপুর গড়ের বর্ধিত অংশ বলা হয়। ঘরবাড়ি নির্মাণ ও জ্বালানি হিসেবে এ বনের কাঠ ব্যবহৃত হয়।
৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন
অবস্থান ও আয়তন :
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় এ বনাঞ্চল অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান গরান বৃক্ষের বনভূমি। এর আয়তন প্রায় ৬ হাজার ১৫ বর্গ কিমি। অন্নধ্যে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলাতেই মোট বনভূমির প্রায় ৯৯% ভাগ অবস্থিত। বাকি অংশ বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলার আওতায় পড়েছে। সুন্দরবনের পশ্চিমে রায়মঙ্গল ও পূর্বে বুড়িশ্বর নদী অবস্থিত। সমুদ্র উপকূল থেকে এটি স্থলভাগের দিকে প্রায় ১২৩ কিমি পর্যন্ত প্রসারিত এবং পূর্ব ও পশ্চিমে এটি প্রায় ১৬১ কিমি লম্বা।
বনাঞ্চল গড়ে ওঠার কারণ
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে এ বিশাল আয়তনের বনাঞ্চল গড়ে ওঠার কারণ হলো বিভিন্ন নদীর মোহনার অবস্থিতি, পলিগঠিত উর্বর কর্দমাক্ত মাটি, সমুদ্রের জোয়ার ভাটা ও লোনা পানি, স্বল্প জনবসতি, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মানুষের স্বল্প বৈষয়িক কার্যাবলী।
সুন্দরবনের বৈশিষ্ট্য
সুন্দর বনে দুই ধরনের অরণ্য দেখতে পাওয়া যায়। যথা-স্বাদু জলের অরণ্য ও লোনা জলের অরণ্য। স্বাদু জলের অরণ্যের মধ্যে সুন্দরী এবং লোনা জলের অরণ্যের মধ্যে গেওয়া বৃক্ষই প্রধান। এছাড়া এ বনাঞ্চলে প্রচুর গড়ান বৃক্ষ জনে। এ বনাঞ্চলের অভ্যন্তর ভাগে অনেক নদী ও খাড়ি বিদ্যমান। ফলে বনাঞ্চলের একাংশ হতে অপর অংশ বিচ্ছিন্ন। সুন্দরবনের নিচু অংশ প্রতিদিন দু’বার করে সামুদ্রিক জোয়ারের পানিতে ডুবে যায়। এ কারণে এ বনাঞ্চলে আগাছার সংখ্যা একেবারেই কম। সুন্দরবনের তিনটি এলাকা বন্য প্রাণীর জন্য অভয়ারণ্য হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। এলাকাগুলো হলো-কটকা-কচিখালী (৫৪৩৯ হেক্টর), হিরন পয়েন্ট (১৭,৮৭৮ হেক্টর) এবং মান্দার বাড়ি (৯০৬৯ হেক্টর)।
সুন্দরবনের বনজ সম্পদসমূহ
এ বনাঞ্চলে সুন্দরী, গেওয়া, রাইন, কেওড়া, বালপাশা, গড়ান, নোনাঝাউ, সিউরা, গুড়া, কাকড়া, বায়েন, ধুন্দল, আমুর, পশুর খলসী, কিরপা, ভোলা, হেতাল, দারুল, গড়াইয়া, তাল ইত্যাদি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তাছাড়া শন, কৃষিপাতা, গোলপাতা, মধু, মোম, ঔষুধী গাছ ইত্যাদি সুন্দরবন হতে সংগ্রহ করা হয়। বাঘ, হরিণ, বানর, ভোদর বনবিড়াল, কুমির, সাপ ও বিভিন্ন প্রকারের পাখি এ বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য জীবজন্তু।
বাংলাদেশের বনজ সম্পদের ব্যবহার
বাংলাদেশের বনজ সম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে মোট দেশজ উৎপাদনে বনজ সম্পদের অবদান ছিল ১.৮৩%। কৃষিখাতে বনজ সম্পদের অবদান ছিল ১০.২%। এ খাতে বর্তমানে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৪.৯১% (১৯৯৫/৯৬ জিডিপির স্থির মূল্যে)। দেশের মোট জনশক্তির শতকরা ২ ভাগ এ খাতে নিয়োজিত রয়েছে। নিচে বাংলাদেশের বনজ সম্পদের বিভিন্নমুখী ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।
১. বনজ সম্পদ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
২. এটি কাগজ, রেয়ন ও মত্ত শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩. বন থেকে আহরিত কাঠ, বাঁশ, বেত, শন ইত্যাদি। ঘরবাড়ি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
৪. বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র তৈরিতে বনজসম্পদ ব্যবহৃত হয়।
৫. বাংলাদেশের কুটির শিল্পের কাঁচামাল বনজ সম্পদ সরবরাহ করে।
৬. পুল, সাঁকো ইত্যাদি নির্মাণে বনজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়।
৭. বন থেকে সংগৃহীত কাঠ নৌকা, লঞ্চ ইত্যাদি তৈরি এবং বিভিন্ন প্রকার নৌযান, ট্রেন, বাস ও ট্রাক ইত্যাদির বডি ও আসন নির্মাণে ব্যবহৃত হয় ।
৮. রেলওয়ের স্লিপার বন থেকে সংগৃহীত কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়।
৯. প্লাইউড, হার্ডবোর্ড ইত্যাদি নির্মাণেও বিভিন্ন প্রকার বনজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়।
১০. বনের মধু খাদ্য ও ওষুধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
১১. মৌচাক থেকে প্রাপ্ত মোম মোমবাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় ।
১২. বারুদ, এসিড, রাবার, ও ভেষজ শিল্পের কাঁচামাল বন থেকে সংগৃহীত হয়।
১৩. বন থেকে সংগৃহীত পশুর মাংস মানুষের উপাদেয় খাদ্য এবং পশুর চামড়া দ্বারা জুতা, ব্যাগ, জায়নামাজ ইত্যাদি সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।
১৪. বাংলাদেশের বনে প্রচুর জীবজন্তু পাওয়া যায়। এদের মধ্যে হরিণ, বাঘ, হাতি, বানর, চিতাবাঘ ইত্যাদির ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক মূল্য প্রচুর
১৫ বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। দেশে প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাব পূরণের ক্ষেত্রে এই মাছের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ।

বনজ সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম
দেশে ব্যাপক বনায়ন ও বন সংরক্ষণ, বন সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাষ্ঠভিত্তিক শিল্প কারখানার, কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীব বৈচিত্র্য, পরিবেশ ও বন্য প্রাণী।
সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা সার্বিক বন উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০ বছর ব্যাপী (১৯৯৫-২০১৫) বন মহাপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। বন মহাপরিকল্পনার তিনটি মূল অঙ্গ, যথা-উৎপাদনমুখী, অংশীদারিত্বমূলক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদির জোরদারকরণ কর্মসূচি।
উক্ত পরিকল্পনার আওতায় বন অধিদপ্তর যে সব কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে নি:শেষিত পাহাড় এবং খাস জমিতে বনের আনুভূমিক বিস্তার ঘটানো; গ্রামীণ এলাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক জমিতে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণ; সরকারি মালিকানাধীন প্রান্তিক ভূমি, যথা- সড়ক, রেলপথ ও সকল প্রকারের বাধের পাশে জনগণের মাধ্যমে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ; বনায়ন ও বন সম্পদ সংরক্ষণে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি গণমাধ্যমে প্রচারণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান; প্রাকৃতিক পরিবেশ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও চিত্ত বিনোদনে বনাঞ্চলের অবদান জনগণকে অবহিতকরণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।
উপসংহার
যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি বহুলাংশে সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশের শ্রম, মূলধন ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে তার সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আজও পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই দেশের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বার্থে এদেশের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।
