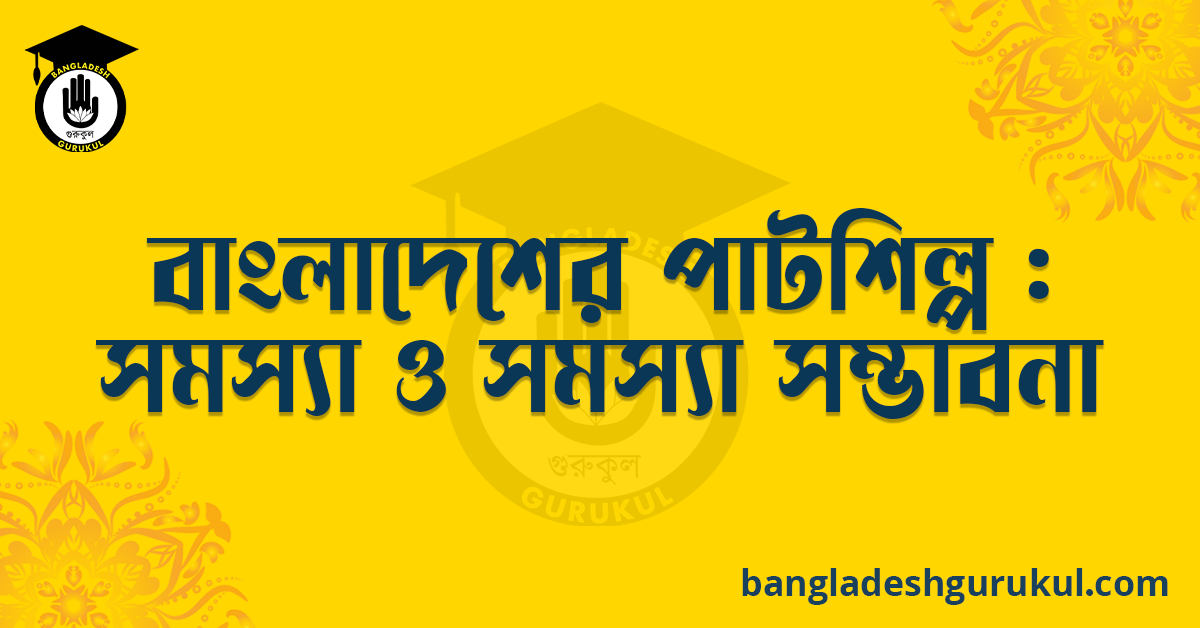বাংলাদেশের পাটশিল্প সমস্যা ও সম্ভাবনা রচনার একটি নমুনা তৈরি করে দেয়া হল। আশা করি এটি শিক্ষার্থীদের কাজে লাগবে। তবে আমরা রচনা মুখস্থ করায় নিরুৎসাহিত করি। আমরা নমুনা তৈরি করে দিচ্ছি একটা ধরনা দেবার জন্য। এখান থেকে ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীদের নিজের মতো করে নিজের ভাষায় রচনা লিখতে হবে।
Table of Contents
বাংলাদেশের পাটশিল্প সমস্যা ও সম্ভাবনা

পাট বাংলাদেশের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। এক সময় পাটকে বলা হতো সোনালী আঁশ। আর তাই পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকলটিও ছিল বাংলাদেশে। অথচ সে পাট আজ আর আগের অবস্থানে নেই। সার্বিক কৃষিখাতের যে নেতিবাচক অবস্থা পাটশিল্পের ক্ষেত্রে এ অবস্থা আরো নাজুক। ইতিমধ্যে আদমজী জুট মিলসহ অনেকগুলো জুট মিল বন্ধ হয়ে গেছে।
সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে প্রতিটি পাটকলই এখন লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই উদ্যোক্তাদেরকে এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে হচ্ছে। কিন্তু এ বন্ধের প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পাশের দেশ ভারত যেখানে নতুন নতুন পাটশিল্প স্থাপন করে বাংলাদেশ থেকে পাট আমদানি করছে সেখানে বাংলাদেশ কেন তার চালু মিলগুলোকে লাভজনক করতে পারবে না।
পাটের গতানুগতিক ব্যবহার হ্রাস পেলেও এর বিকল্প ব্যবহারও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো আমাদের সরকার পাটের বিকল্প ব্যবহারের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করেই একের পর এক পাটকল বন্ধের ঘোষণা দিচ্ছে যা বেকারত্ব, দারিদ্র্য আর সামাজিক অস্থিরতার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।
বাংলাদেশে পাটশিল্পের বিবর্তন
বাংলাদেশের পাটশিল্পের সূচনা ১৯৫২ সালে এবং এই সূচনা বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাদের দ্বারা এ দেশে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম পাটশিল্প স্থাপিত হয় এবং বিশ্ব বাজারে পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ সেরা প্রমাণিত হয়, দেশে পাটপণ্য শ্রেষ্ঠ রপ্তানির আয়ের খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, দেশের পাটশিল্পে প্রায় ২ লাখ শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান হয় ।
কিন্তু ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় এবং সেই বছর ডিসেম্বরে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এক শ্রেণীর পাটশিল্প স্থাপনকারী অস্থানীয় শিল্পপতিরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। ফলে এই সকল পাটশিল্প ১৯৭১-৭২ সালে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। অস্থানীয়দের দ্বারা স্থাপিত পাটকল মালিকরা দেশ ত্যাগ করার কারণে সকল পাটকল ‘পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে।
অতঃপর তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক দর্শনে পরিচালনার অংশ হিসেবে ঐ সকল ‘পরিত্যক্ত পাটকলের সাথে স্থানীয় বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের দ্বারা স্থাপিত পাটকলসহ দেশের সকল পাটকলকে ১৯৭২ সালে ‘রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়। এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থাপনার বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) স্থাপন করে দেশের সকল পাটকল পরিচালনার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। উক্ত কর্পোরেশনের মাধ্যমে পরিচালিত দেশের পাটকলসমূহ ক্রমাগত লোকসান দিতে থাকে।

জিয়া সরকার ১৯৭৬ সালে পাটশিল্পের ক্রমাগত লোকসানজনিত কারণ সম্পর্কে অবহিত হয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি ‘ইন্সপেকশন কমিটি’ গঠন করেন। ঐ কমিটির রিপোর্টের আলোকে “জিয়া সরকার’ পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশক্রমে পাটকলসমূহকে ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
১৯৭৯ সালে জিয়া সরকার পাট শিল্পখাতকে বিরাষ্ট্রীয়করণ কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৭৯-৮০ এর মধ্যে ৭টি পাট সুতাকল বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করেন যার মধ্যে বাংলাদেশীদের দ্বারা স্থাপিত ৩টি পাট-সুতাকল পূর্বতন দেশীয় মালিকদের নিকট হস্তান্তর করেন, বাকি চারটি বিক্রয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশীদের নিকট হস্তান্তর করেন এবং পাটশিল্প স্থাপন বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নিকট উন্মুক্ত করে দেন।
১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান শাহাদাতবরণ করলে জিয়া সরকারের শিল্প উপদেষ্টা শফিউল আজম পরবর্তী সরকারের আমলেও উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত হন এবং পাটশিল্প বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি অব্যাহত রাখেন। ১৯৮২-৮৪ সালে বাংলাদেশীদের দ্বারা স্থাপিত পাটকলসমূহের মধ্যে ৩৫টি পাটকল পূর্বতন বাংলাদেশী মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। কিছুদিন পর সফিউল আজম উপদেষ্টার পদ থেকে বিদায় হন এবং পাটকল বিরাষ্ট্রীয়করণ কার্যক্রম আর অগ্রসর হয়নি।
১৯৮২ সাল থেকে পাটশিল্প সরকারি-বেসরকারি দুটি খাতে পরিচালিত হতে থাকে। বিরাষ্ট্রীয়করণের পর ১৯৮৩-৮৫ সময়ে বিরাষ্ট্রীয়কৃত বেসরকারি মিলসমূহ মুনাফা অর্জন করে, যদিও ঐ সময়ে সরকারি খাতের পাটকল (বিজেএমসির মাধ্যমে পরিচালিত) ক্রমাগত লোকসান দিতেই থাকে।
তৎকালীন সরকার তখন পাটশিল্প সম্পর্কে যে সকল নীতি অবলম্বন করে তাতে সরকারি খাতে পাটকলগুলো আরো বেশি লোকসানে পতিত হয় এবং বেসরকারি খাতের পাটকলসমূহ লাভজনক থেকে লোকসানে পতিত হয়। এমতাবস্থায় সরকার সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের পাটশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান পন্থা অবলম্বন করে। এতে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হতে থাকে।
সরকারের রাজস্ব খাত থেকে এরূপ বিপুল অর্থ ব্যয় রোধকল্পে ১৯৯০ সালে বিশ্বব্যাংক একটি সমীক্ষা পরিচালনাপূর্বক পাটশিল্পকে লাভজনক করার একটি সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঐ সংস্কার কর্মসূচি ১৯৯২ সালে শুরু হয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে শেষ হয়। এতে বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত ২৫০ মিলিয়ন ডলার প্রদানের অঙ্গীকার থাকলেও মাত্র ৪৫ মিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়।
মেয়াদান্তে দেখা গেল, বিশ্বব্যাংকের ফর্মুলায় গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি বাংলাদেশের সরকারি খাত বা বেসরকারি খাতের পাটশিল্পকে স্বাক্ষর করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বব্যাংকও এই ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর বিশ্বব্যাংক, পাট খাতের সরকারি (বিজেএমসি) ও বেসরকারি (বিজেএমএ ও বিজেএসএ) উভয় খাত মিলিতভাবে পাট মন্ত্রণালয়ের ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নতুনভাবে আরেকটি পাটশিল্প সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা কামনা করার পরামর্শ দেয়।
সে উদ্দেশ্যে পাট মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৯৭ সালের অক্টোবরে ঐ রিপোর্ট পার্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু পাট মন্ত্রণালয় তথা সরকার উক্ত রিপোর্টের ওপর কোনোরূপ কার্যক্রম এ যাবত এগ্রহণ করেনি। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাংক সংস্কার কর্মসূচি সমাপনের পর ১৯৯৭ সালে বিশ্ব বাজারে পাটজাত পণ্য রপ্তানির দাম অসম্ভবভাবে হ্রাস পায়, ফলে সকল পাটকলই লোকসানে পতিত হয়।

সরকার আবার ১৯৮৮ সালে রাজস্ব খাত থেকে এই পণ্য রপ্তানিতে নগদ আর্থিক সহায়তা আরম্ভ করে, এই নগদ আর্থিক সহায়তা লোকসানের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। ফলশ্রুতিতে সকল পাটকল কমবেশি লোকসান দিতে থাকে। বেসরকারি মিলসমূহের মধ্যে অনেক মিল রুগ্ন হয়ে পড়লো কোনো কোনো মিল বন্ধ হয়ে গেল।
কিন্তু এরূপ লোকসান অবস্থা সরকারি মিলেও থাকার কারণে সরকারি মিলসমূহ চালু রাখার স্বার্থে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সরকারি মিলকে (বিজেএমসি) বাংলাদেশ সরকার বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে ৫০৫ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করে, কিন্তু বেসরকারি মিলের লোকসান অবস্থার অনুরূপ পরিস্থিতিতে সরকার কোনোরূপ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেনি।
বাংলাদেশের পাটশিল্পের সমস্যা
বাংলাদেশের পাটশিল্প আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। যেমন— প্রথমত, দেশের সরকারি বেসরকারি প্রায় সবগুলো জুট মিলই বর্তমানে লোকসানি মিলে পরিণত হয়েছে। এসব মিল বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় এগুলো নিয়ে উভয় সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।
দ্বিতীয়ত, দেশে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্লাস্টিকসহ অন্যান্য বিকল্প আবিষ্কৃত হওয়ায় পাটের চাহিদা বেশ হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য সরকার পলিথিন বন্ধ করায় এক্ষেত্রে কিঞ্চিত সম্ভাবনা জেগে উঠে। কিন্তু সে সম্ভাবনাকেও আমরা এখন পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারিনি।
তৃতীয়ত, আমাদের পাটকলগুলোতে সিবিএ নামের দৈত্যের প্রভাবে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা যাচ্ছে না। ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক, অন্য দুর্নীতিসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত মিলগুলো একের পর এক বন্ধ হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের পাট আমদানি করে ভারত একের পর এক নতুন নতুন জুট মিল স্থাপন করছে।
চতুর্থত, আমাদের দেশে পাট উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে ভারতের অনুন্নত বীজ উৎপাদনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাছাড়া ন্যায্য দাম না পেয়ে কৃষকরাও পাট উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।
পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা
বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলে খ্যাত পাটশিল্পের অবস্থা বর্তমানে খুবই করুন। একের পর এক জুট মিল ও স্পিনিং মিল বন্ধ ঘোষণা বাজারে পাটের নিম্নমূল্য এবং সরকারি অনীহার কারণে পাটের চাষও অনেক হ্রাস পেয়েছে। এবার পাটের মোট উৎপাদন লক্ষ্য যা নির্ধারিত হয়েছে, কোনোভাবেই তা অর্জিত হওয়ার কথা নয়। তারপরও যা উৎপাদিত হবে অভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় তা হবে অনেক বেশি।
এক খবরে জানা গেছে, চালু সরকারি-বেসরকারি মিলগুলোর মোট চাহিদা ২৩ লাখ বেলের মতো। এবারের সম্ভাব্য উৎপাদনের সঙ্গে গত বছরের ৫ লাখ বেল মজুদ যোগ করলে মোট পাটের পরিমাণ ৫০ থেকে ৫৫ লাখ বেলের কাছাকাছি দাঁড়াবে। এ অবস্থায় উপযুক্ত দামে ও ব্যবস্থায় পাট কেনার পদক্ষেপ না নিলে ব্যাপকহারে পাট পাচার হয়ে যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা পাটের দামে চাঙ্গাভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮ মাসের তুলনায় ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের একই সময়ে ৬ লাখ ২১ হাজার বেল বেড়েছে। একইভাবে পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণমুখী। এই সুযোগটি আমরা কতটা কাজে লাগাতে পারবো তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে।
পাটের আবাদ-উৎপাদন ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দেয়া হচ্ছে, একথা বলার উপায় নেই। বরং এমন ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে যাতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পতিত হয়। আদমজী জুট মিলসহ ৫টি জুট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাটের অভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হয়ে পড়েছে।
পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়বেই। পক্ষান্তরে পাটের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে পাটের আবাদ- উৎপাদন বাড়ছে। পাট উৎপাদন বাড়ানোর জন্য চাষীদের নানাভাবে উৎসাহিত ও সহযোগিত করা হচ্ছে। নতুন নতুন জুট মিলও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেগুলো উৎপাদনে গেছে। আমাদের আবাদ-উৎপাদন কমছে, মিল বন্ধ হচ্ছে আর ভারতে দুই-ই বাড়ছে।
ভারত আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বটে কিন্তু বাংলাদেশের পাটের ওপর তার নির্ভরশীলতা প্রবল। বাংলাদেশের পাটের শীর্ষ ক্রেতা ভারত। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ভারত বাংলাদেশ থেকে ৩৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের কাঁচা পাট আমদানি করেছে।
বলা হয়ে থাকে, ভারত প্রতি বছর যে পরিমাণ পাট বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি পাট চোরাপথে টেনে নেয়। ভারতের ৭৫-৮০টি জুট মিল কোনো না কোনোভাবে বাংলাদেশের পাটের ওপর নির্ভর করে সারা বছর চালু থাকে। পাটের এই উৎসটি বন্ধ হলে এগুলোর অধিকাংশই রাতারাতি বন্ধ হয়ে যাবে।
সরকারি খাতের পাশাপাশি আমাদের বেসরকারি খাতের অবস্থাও সঙ্গীন ও শোচনীয়। বেসরকারি জুট নিল অ্যাসোসিয়েশনের অনেক মিলই এখন বন্ধ। এই খাতে হস্তান্তরিত ৩৫টি জুট মিলের ৩০টি এবং ১০টি স্পিনিং মিল বন্ধ বলে জানা গেছে। কাঁচা পাটের পর্যাপ্ত প্রাপ্তি সত্ত্বেও জুট মিলগুলো এই করুণ ও মর্মান্তিক দশায় পতিত হলো কেন?
বাংলাদেশের পাটশিল্পের সম্ভাবনা
আমরা দীর্ঘদিন ধরে পাটের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার শুনছি। কিন্তু সেই অঙ্গীকার কার্যকর হতে দেখছি না। উল্টো পাটের আবাদ-উৎপাদন-রপ্তানি কমছে। অনিশ্চয়তার অন্ধকারে পাটের ভবিষ্যৎ হারিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো মহলের দাবি, এখনও বৈদেশিক মুদ্রার ৩০ শতাংশের বেশি পাট থেকে আসে। পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদাও বহির্বিশ্বে ক্রমাগত বাড়ছে। সুতরাং এই খাতে আয় বাড়ানোর আরো সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও পাটের বিপুল সম্ভাবনার কথা বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন। যেমন-
ক. কাঁচা পাট থেকে কাগজের মণ্ড তৈরির প্রযুক্তি আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী আবদুল খালেক আমাদের মাঝে আশার আলো জাগিয়েছিলেন। কাগজের উৎকর্ষ কাঁচামাল হিসেবে পাটের সম্ভাবনা বিপুল। বলা হয়ে থাকে, মণ্ড তৈরিতে পাটের ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে এই খাত থেকে প্রতি বছর আমাদের বাজেটের সম পরিমাণ অর্থ যোগান দেয়া সম্ভব। এতে কাগজ আমদানি করতে আমাদের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তা লাঘব হবে এবং কৃষকও তার পাটের ন্যায্যমূল্য পাবে।
খ. পাটের মিহি তত্ত্বসহ বিভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কারের ব্যাপারে দীর্ঘদিন যাবতই নানা সম্ভাবনার কথা শোনা
যাচ্ছে। বলা হয় যে, পাটের এই মিহি তত্ত্ব ব্যবহার করে উন্নতমানের কাপড় উৎপাদন সম্ভব।
গ. পলিথিন ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগের ব্যবহারের কথা সবারই জানা। সপ্তায় সহজলভ্য করে পলিথিনসহ প্লান্টিক ও নাইলনের বিকল্প হিসেবে পাটের ব্যাগকে বাজারে ছাড়তে পারলে এ শিল্প অবশ্যই তার হৃতগৌরব ফিরে পেতে পারে ।
ঘ. রপ্তানি ক্ষেত্রেও পাটের চাহিদা একেবারে কম নয়। ভারত, চীন, মিশরসহ অন্যান্য আমদানিকারক দেশসমূহে বাংলাদেশী পাটের বেশ চাহিদা রয়েছে।

বাংলাদেশের পাটশিল্পের জন্য সুপারিশমালা
দেশের বেসরকারি খাতের (বিজেএমএ) অনেক মিল আর্থিক সংকটের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে সরকারি (বিজেএমসি) এবং বেসরকারি খাতের (বিজেএমএ) অনেক জুটমিল বন্ধ আছে। বিজেএমসি পরিচালিত মিলসমূহের মধ্যে দেশের বৃহত্তম জুট মিল আদমজী পাটকল ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আরো ৭টি মিল বেসরকারি খাতে বিক্রয়-হস্তান্তর প্রক্রিয়ার জন্য অনেক দিব যাবৎ বন্ধ রয়েছে। বেসরকারি খাতে প্রায় ২০টি মিলই বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। এহেন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে যে সকল নীতি-নির্ধারণী বিবেচনা করা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ
ক. সরকারি মালিকানায় বিজেএমসির মাধ্যমে পরিচালিত যে সকল পাটকল বেসরকারি খাতে হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে, তা বেসরকারি ক্রেতা উদ্যোক্তাদের নিকট সত্ত্বর হস্তান্তর প্রক্রিয়া সমাধান করা।
খ. বিজেএমসির মাধ্যমে পরিচালিত বাকি মিলসমূহের প্রাইভেটাইজেশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। সরকারি মিলসমূহ বেসরকারি খাতে যতদিন হস্তান্তরিত না হয়, সে সময় সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মিলসমূহের মধ্যে দুই রকম বা বৈষম্য নীতি পরিহার করা, দু খাতের মিলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করা ।
গ. পাটশিল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্বব্যাংকের সুপারিশক্রমে পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যে পুনর্বিন্যাসকৃত পাটশিল্প সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং যা পাট মন্ত্রণালয়ে জমা আছে, তা বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ জরুরিভাবে গ্রহণ করা দরকার। প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন পাটশিল্পকে পুনর্জীবিত করবে।

উপসংহার
বাংলাদেশের পাটশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের নানা পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলাই হচ্ছে, আসলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অথচ উল্লিখিত সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোতে পাটের ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে পার্ট রাজস্ব ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে শীর্ষে উঠে আসতে পারে। এই সম্ভাবনা কার্যকর করার যথোচিত উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না কেন, সেই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই।
সরকার কি পাট বাঁচানোর জন্য, পাটের গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য, পাটের সম্ভাবনাসমূহ কার্যকর করার জন্য আলাদা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নিতে পারে না? ভারতকে পাটের রাজা বানানোর যে ষড়যন্ত্র অনেক আগেই শুরু হয়েছে, সে ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। একদিন বাংলাদেশই পাটের রাজা ছিল। আবারও রাজার আসনে তাকে অধিষ্ঠিত করতে হবে।