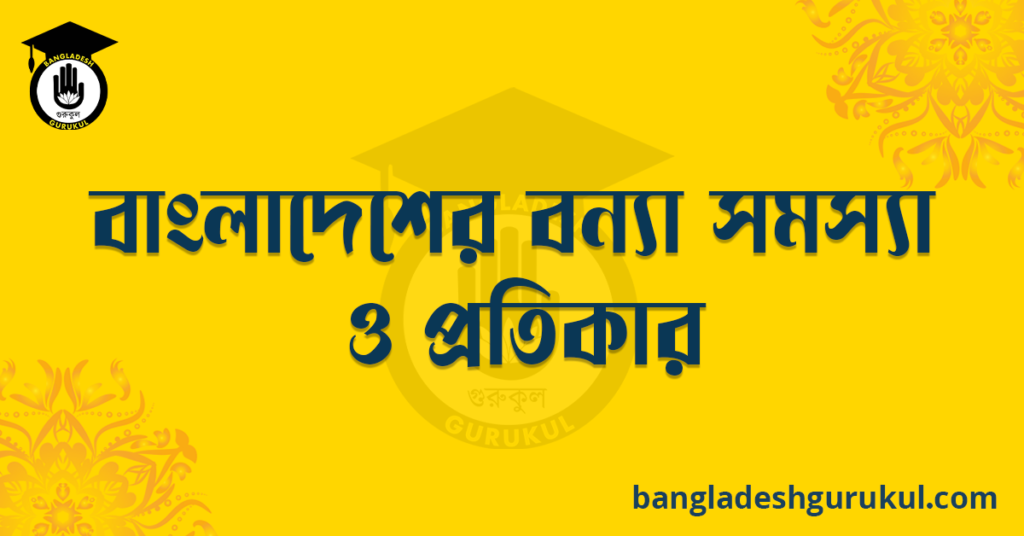বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও প্রতিকার রচনার একটি নমুনা তৈরি করে দেয়া হল। আশা করি এটি শিক্ষার্থীদের কাজে লাগবে। তবে আমরা রচনা মুখস্থ করায় নিরুৎসাহিত করি। আমরা নমুনা তৈরি করে দিচ্ছি একটা ধরনা দেবার জন্য। এখান থেকে ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীদের নিজের মতো করে নিজের ভাষায় রচনা লিখতে হবে।
ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। বাংলাদেশে বন্যা নতুন কিছু নয়। দু-এক বছর পরপরই আমরা বন্যার তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করি। অবস্থানগত কারণেই আমাদের পক্ষে কখনোই সম্পূর্ণরূপে বন্যামুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা যদি পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করি তাহলে ভবিষ্যতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলেও সীমিত রাখা যাবে । তাই বন্যার কারণ এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।
Table of Contents
বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও প্রতিকার
প্রেক্ষাপট
বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে প্রায় ৩০টির মতো বড় ধরনের বন্যা সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০০ সালের বন্যা এবং সর্বশেষ ২০০৪ সালের ভয়াবহ রেকর্ড সৃষ্টিকারী বন্যার কথা উল্লেখ করা যায় । বাংলাদেশের মানুষ বন্যার করাল গ্রাস থেকে মুক্তি চাইলেও মুক্তি পাচ্ছে না। সুদীর্ঘকালের এ বন্যার পীড়নের কারণও কম নির্দেশিত হয়নি। বাংলাদেশে বন্যার অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করা হয় অতিবৃষ্টিকে।
বন্যার জন্য নদীর অনাব্যতা এবং উজানের পানিও অনেকাংশে দায়ী। বাংলাদেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩২০ মিলিমিটার। এ বৃষ্টির শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে । বাংলাদেশের ভূমি সমতল, ফলে বৃষ্টির এই পানি সহসা সরে যেতে পারে না।
বাংলাদেশে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২৩০টি নদী রয়েছে। বহু বছর ধরে নদীগুলোতে ড্রেজিং না করার ফলে এর পানি ধরে রাখার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে অতিবৃষ্টি হলে নদীসমূহের দুকূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। তবে এ দেশে বন্যার অন্যতম কারণ উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢল ।
হিমালয় থেকে নেমে আসা বিপুল জলরাশি ভারত ও নেপালের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মাধ্যমে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় । প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ কিউসেক পানি এ প্রধান তিনটি নদীর মাধ্যমে প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রবল চাপের মাধ্যমে বন্যার সৃষ্টি করে ।
বন্যার কারণ ও স্বরূপ অনুসন্ধান
বিশেষজ্ঞরা বন্যার জন্য বেশ কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন।
ক. প্রাকৃতিক কারণ
১. পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার সকল পানি সমুদ্রে যাওয়ার যে একমাত্র পথ, তারই ভাটি এলাকায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান।
২. একদিকে পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে বনাঞ্চলসমূহ দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যেমন ক্রমশ বাড়ছে, তেমনি হিমালয়ে আগে যে বিপুল পরিমাণ পানি বরফ হয়ে জমা থাকতো, তাও ক্রমে গলে নিচে নেমে আসছে।
৩. গত আড়াই দশকে পলি জমে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের স্বাভাবিক পানি পরিবহন ক্ষ হ্রাস পেয়েছে। ভারত কর্তৃক বিভিন্ন নদীতে বাঁধ নির্মাণ ও একতরফা পানি অপসারণের ফলে মৌসুমে বাংলাদেশের নদ-নদীর স্রোত এতোই কমে যায় যে, তার পক্ষে পলিমাটি ঠেলে নিয়ে সম্ভব না । ফলে, দেশের নদীসমূহ ক্রমশই ভরাট হয়ে যাচ্ছে। যেমন—হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে ৩০ m আগে পদ্মা নদীর যে গভীরতা ছিল এখন তা অন্তত ৮০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ব্রহ্মপুত্রসহ অন নদ-নদীরও প্রায় একই অবস্থা। ফলে এখন নদীসমূহ আর বন্যার পানি টেনে নিতে পারছে না।
৪. বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে সমুদ্রের পানির। বৃদ্ধিও বন্যার বিশেষ কারণ।
৫ পদ্মা-মেঘনার নির্গম বা সাগর সঙ্গমস্থলে যে বিশাল স্থলভূমি জেগে উঠেছে সেটাও পালি প্রবাহকে অনেকাংশে বাধাগ্রস্ত করছে।
৬. ভূ-গর্ভের অগভীর স্তরে পানির প্রবাহ ( Sub Surface water circulation) বৃদ্ধি ও বন্যার কারণ।
৭. বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সমুদ্রের পানি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্বদিকে ঠেলে বঙ্গোপসাগরের পূর্বাঞ্চলে স্তূপীকৃত চেষ্টা করে । বর্ষাকালে মৌসুমী বায়ুর কারণে পানির উজান চাপ একটি সার্বক্ষণিক ব্যাপার।
৮. বর্ষাকালে বাংলাদেশের সমুদ্রে প্রচুর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সকল নিম্নচাপ সাময়িকভাবে কন পরিস্থিতিকে আরো গুরুতর করে তোলে। তাছাড়া নিম্নচাপ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যা বন্যার পানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় ।
খ. কৃত্রিম কারণ
১. অবকাঠামো নির্মাণ :
মানুষ জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য নদী অববাহিকায় ব্রিজ, জলবিদুৎ উৎপাদন করার নিমিত্তে বাধে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভেড়িবাধ নির্মাণ করেছে। বং নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। তাছাড়া নদীর তীর বরাবর ভেড়িবা নির্মাণের ফলে নদীর পানি অববাহিকায় প্লাবিত হতে পারে না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে न তলদেশ পলি-বালি সঞ্চিত হতে হতে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।
২. অরণ্য নিধন
গঙ্গা, যমুনা নদীর উৎসস্থলে ব্যাপকভাবে বন উজারকরণ বাংলাদেশে বন্যার আরেকটি কারণ। স্বাভাবিক অবস্থায় বৃষ্টির পানি নদী-নালায় আসার আগে বনাঞ্চলের গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়, ঝরা পাতা ও শিকড়ে বাধা পেয়ে মোট বৃষ্টিপাতের ৫০-৫৫ ভাগ পানি তৃগর্ভে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাপক হারে বনাঞ্চল কাটার ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের সিংহভাগ পানি বাধা না পেয়ে নদীতে চলে আসায় পানিপ্রবাহ বেড়ে যায় এবং বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়া নদীর উৎসে বনাঞ্চল কেটে ফেলার কারণে বিরাণ এলাকার প্রভূত পরিমাণ পলিমাটি বয়ে এনে প্রবাহ পথ বন্ধ করে দেয় ।
৩. গঙ্গা নদীর ফারাক্কা বাঁধ
বাংলাদেশের বন্যার আরেকটি প্রধান কারণ হলো পশ্চিমবঙ্গে ফারাক্কা বাঁধ। এ বাঁধ নির্মাণের আগে ভাগীরথী নদীতে বর্ষাকালে যেখানে প্রতি সেকেন্ডে ১,৩০,০০০ ঘনফুট পানি প্রবাহিত হতো, তা বাঁধ নির্মাণের পরে দাঁড়ায় ৮০,০০০ ঘনফুটে।
এই হ্রাসপ্রাপ্ত ৫০,০০০ ঘনফুট পানিপ্রবাহ অতিরিক্ত হিসেবে বন্যার প্রকোপ বাড়িয়ে তুলেছে। তাছাড়া ভারত প্রতি বছর শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় পানি আটকে রেখে বর্ষা মৌসুমে সকল গেট একসঙ্গে খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালায়, যার ফলে বাংলাদেশের বন্যার সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পায় ।
৪. সামুদ্রিক জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস
বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী বর্ষাকালে কোটি কোটি কিউসেক পানি দেশের ওপর দিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এ বিপুল পরিমাণ পানি খুব সহজেই বঙ্গোপসাগরে মিশতে পারে না। কারণ নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট জোয়ারের পানির চাপ নদীর পানির চাপের চেয়ে ৫ গুণ বেশি। অর্থাৎ জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য নদীর পানিপ্রবাহ বাধা পেয়ে সাগরে পতিত না হয়ে ওভার ফ্লো হয়ে বন্যার সৃষ্টি করে।
এছাড়া বিজ্ঞানীরা বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের আরেকটি কারণ দাঁড় করিয়েছেন, তা হলো গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া’। গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া তথা তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য পর্বত শিখরে ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে নদীর পানির উচ্চতা ও প্রবাহ বৃদ্ধি করে, এই বরফ গলা পানি বৃষ্টির পানির সঙ্গে একত্রে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ।
৫ ভূমিক্ষয়
অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, দালান-কোঠা তৈরি প্রভৃতি কাজে নিম্নভূমির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ভূমিক্ষয় হয়ে যায়। তাছাড়া সাম্প্রতিককালের ভূমিকম্পনের ফলেও অতিরিক্ত মাটিক্ষয় হয়ে নদীমুখ বন্ধ ও দিক পরিবর্তন করে ফেলেছে। এতে নদীতে পানি ধারণক্ষমতা কমে যাওয়ায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
বন্যা সমস্যার প্রতিকার
বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগ থেকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কার্যত তেমন কিছু করা হয়নি। বাঁধের মাধ্যমে এ যাবৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণের কিছুটা চেষ্টা করা হলেও তেমন কোনো সাফল্য অর্জিত হয়নি। সাম্প্রতিক কালের বন্যার তীব্রতা ও ব্যাপকতা সে কথাই প্রমাণ করে।
ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বন্যাকে স্থায়ীভাবে প্রতিরোধ করা না গেলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবকাঠামোগত ও অ-অবকাঠামোগত নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বন্যার ভয়াবহতা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে। বন্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তিন ধরনের পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে
ক. তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা,
খ. দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা ও
গ. সমন্বিত ব্যবস্থা।
ক. তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাসমূহ
১. প্রাক-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা
বন্যা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাক-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রযুক্তিগতভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ সক্ষম। এক্ষেত্রে ভূ-তাত্ত্বিক ও আঞ্চলিক পরিবাহের মাধ্যমে সর্তকীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে। ফলে জান- মাল যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষা পাবে।
২. ত্রাণব্যবস্থা সক্রিয়করণ
বন্যা-উত্তর ত্রাণব্যবস্থা সক্রিয় রাখার উদ্দেশ্যে ও ত্বরিত সাহায্য সরবরাহের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে যথেষ্ট ত্রাণসামগ্রী মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
পানিবন্দি এলাকায় প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি জরুরি অশ্রেয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি স্কুলগৃহকে বহুতলে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, যা অন্তত ৩,০০০ লোক ধারণ করতে পারে।
৪. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন
সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে বন্যা প্রতিরোধের জন্য আরো কার্যকর ও সক্রিয় হতে হবে। এক্ষেত্রে একটি দুর্যোগ সংক্রান্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। স্থাপন করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি বন্যাসহ সকল দুর্যোগ সম্পর্কে তথ্য আহরণ, সংরক্ষণ 1 প্রচার এবং দুর্যোগ প্রতিরোধক কর্মসূচি ও গবেষণা পরিচালনা করবে ।
৫. অন্যান্য ব্যবস্থা:
এছাড়া সরকার ও জনগণের বন্যার আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করা, ঘরবাড়ির ভিটে উঁচু করা ও গুচ্ছগ্রাম গড়ে তোলা, বন্যার উপযোগী ধানের উদ্ভাবন ও চাষ করা ইত্যাি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।
খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা :
বন্যা প্রতিরোধ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহ হলো মুখ্য। দীর্ঘ ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ
১. রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত
প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই আমাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি নিতে হবে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নেপাল, ভারত, ভুটান ও বাংলাদেশকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর ব্যবস্থার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
২. বাঁধ নির্মাণ
বন্যার পানি প্রবেশের উৎসমুখ বন্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও তিস্তা— এ তিনটি নদীতেই শুধু বাঁধ নির্মাণ নয়, উক্ত তিনটি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন খাঁড়ির মুখে বাঁধ দিতে হবে। এতে বাংলাদেশের পক্ষে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
৩. পোল্ডার নির্মাণ
দেশের উপকূল ভাগে স্থাপিত ৭০০ স্বয়ংক্রিয় জোয়ারবিরোধী গেটের মতো কাঠামো দ্বারা সাগরের জোয়ার অনুপ্রবেশ রোধ এবং জলাবদ্ধ এলাকায় পোল্ডার নির্মাণ করে পানি পাম্প করে বের করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
গ. সমন্বিত ব্যবস্থা
ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীনকে নিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক পরিকল্পন নিতে হবে। দেশে জাতীয় ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে জরুরি ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে পুনরায় বন্যা না দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে ।
এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আরো কতিপয় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে
১. প্রধান নদী ও শাখানদীগুলোর মুখ খনন করা, যাতে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারে।
২. নদীর তীর বরাবর উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ করা, যাতে পানি নদী খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
৩. নদীর তলদেশ খনন করা; যাতে পানি বেশি পরিমাণে দ্রুত সাগরে চলে যেতে পারে ।
৪. নদী ছোট বা বড় যা-ই হোক না কেন, নদীর মুখ বন্ধ না করে রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ ।
৫. নদীর উৎসস্থলে ও অববাহিকায় ব্যাপক ঘন অরণ্য সৃষ্টি করে বৃষ্টির বা বরফ গলা পানি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করা।
৬. নদীর উৎসস্থলে ও অববাহিকায় জলাধার নির্মাণ করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পানি পরে সেচের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।
৭. Flood Action Plan-এর প্রস্তাবিত সমীক্ষাসমূহ পুনরায় যাচাই করা, যাতে তা জাতীয় স্বার্থে এবং চাহিদার উপযোগী করে তোলা যায় ।
বন্যার সাথে যেহেতু আমাদের সহাবস্থান করতে হবে, সেহেতু বন্যাকে মেনে নিয়ে মানুষ তাদের ক্ষুদ্র সম্পদ নিয়ে যাতে বন্যার সময় নিরাপদ থাকতে পারে সে বিষয়টি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। যে বিষয়টি শুকনা মৌসুমে করা যায় তা হলো, বন্যাপ্রবণ এলাকায় সর্বোচ্চ বন্যা লেভেলের চেয়ে উঁচু মাঠ তৈরি করে (দক্ষিণাঞ্চলের কিল্লার মতো) বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
এখানে বিশুদ্ধ পানি ও সুষ্ঠু পয়ঃব্যবস্থা থাকবে। খাদ্য ও ওষুধের মজুদ থাকবে। প্রথমে প্রতি ইউনিয়নে পরে প্রতি গ্রামে একটি করে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। আমাদের সস্তা জনশক্তি নির্মাণ কাজে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া
- সুন্দরবন ও পাহাড়ি এলাকার মতো উঁচু খুঁটির ওপর ঘরবাড়ি নির্মাণ করার পদ্ধতি চালু করতে হবে।
- প্রথমে শহর ও পরে গ্রামকে উঁচু বাঁধ দ্বারা ঘেরাও করতে হবে।
- সস্তা শ্রমশক্তি ব্যবহার করে পুকুর, নালা, খাল, বিল খনন করে সেচের পানি সংরক্ষণ করতে হবে ।
- নদী খনন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হলেও পদ্মা, মেঘনা, যমুনা তিনটি প্রধান নদীকে নিয়মিত ড্রেজিং করে পানি সংরক্ষণের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। খননকৃত মাটি দ্বারা উঁচু বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র বানাতে হবে । নদীতীরকে স্থায়ী মজবুত কাঠামো দ্বারা সংরক্ষিত করলে নদী স্রোত বৃদ্ধি হয়ে পলি জমা বন্ধ হবে। যেরূপ স্থায়ী কাঠামো যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় করা হয়েছে।
- বেড়িবাঁধ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
- প্রতি বছর অল্প করে হলেও নদীর তীর রক্ষায় স্পার, গ্রোয়েন, পারকোপাইন, গ্যারিয়ন ইত্যাদি নিক্ষেপের পাশাপাশি শহর এলাকায় ব্রিজ এবাটমেন্ট বা পিয়ারের মতো স্কাউর ডেপথের নিচ পর্যন্ত কংক্রিটের দেয়াল নির্মাণ করা উচিত।
- পূর্বাভাস ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে, যাতে মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা অববাহিকায় অতি বৃষ্টি হলে তা আমাদের জাতীয় প্রচার মাধ্যমে জানানো উচিত। আগারগাঁওয়ে স্থাপিত রাডারটির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২৪ তলা আইডিবি ভবনে স্থানান্তর করা উচিত । এছাড়া দিনাজপুর অঞ্চলে একটি রাডার কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন ।
- কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বন্যা উপযোগী করা প্রয়োজন। কাঠ বা প্লান্টিকের ভাসমান বীজতলা তৈরি করা প্রয়োজন।
- ব্যাপক বনায়ন প্রয়োজন।
উপসংহার
বন্যা নামক সর্বগ্রাসী দৈত্যের ভয়ে দেশবাসী সর্বদা শঙ্কিত। বন্যার ভয়াবহ তাণ্ডবলীলায় প্রতি বছর মৃত্যুবরণ করে হাজার হাজার মানুষ। পানিতে ভেসে যায় অসংখ্য ঘরবাড়ি ও গবাদিপশু । পানিবন্দি হয়ে এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হয় লাখ লাখ মানুষ। বিনষ্ট হয় হাজার হাজার একর জমির ফসল। সর্বোপরি ভেঙে যায় কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড এবং নেতিবাচক প্রভাব পড়ে লেনদেনের ভারসাম্যে । সুতরাং এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে দেশবাসীর মুক্তির জন্য সরকারের বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।
আরও দেখুনঃ