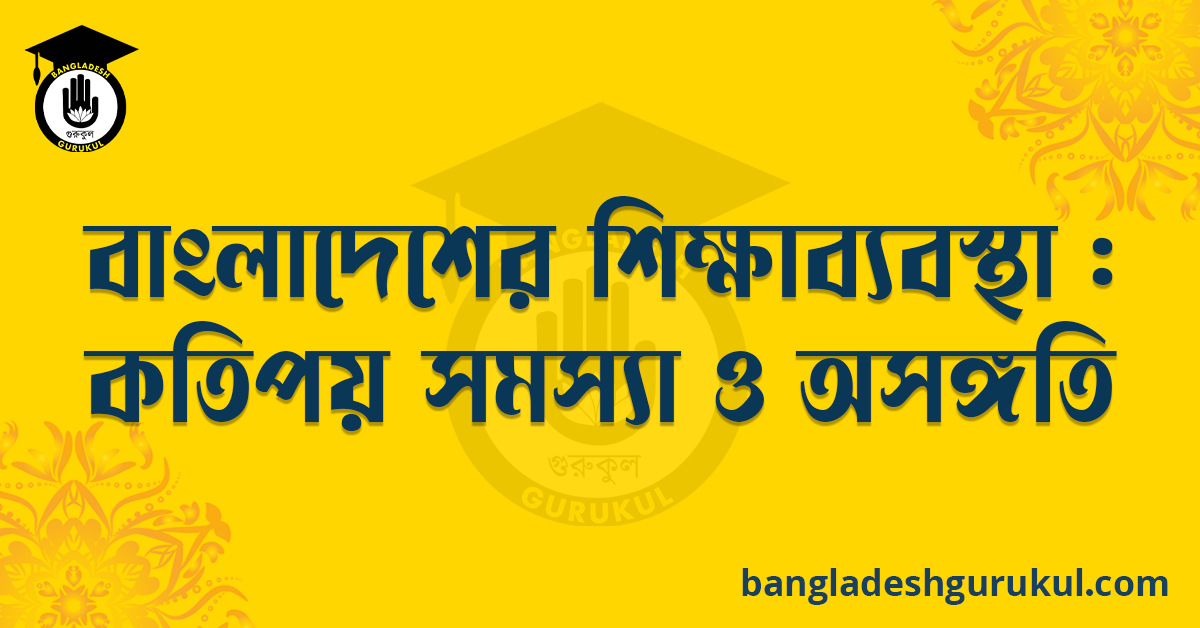বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক আলোচনা হয়েছে এবং শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক দেখা দেয়। তবে সার্বিকভাবে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করলে এতে অসংখ্য সমস্যা ও অসঙ্গতি চোখে পড়ে। আর এ কারণেই অব্যাহত প্রচেষ্টা আর কর্মসূচির পরও আমরা শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছি না।
দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক এখনো নিরক্ষর। এমনকি যে ৬৫ শতাংশ লোককে শিক্ষিত বলা হয় প্রকৃতার্থে তাদের সকলকে শিক্ষিত বলা যায় না। এমনকি শিক্ষার গুণগত মানও এখানে খুবই নিম্ন। সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষার প্রতি যে মোহ তা কাটিয়ে ওঠার সৌভাগ্য এখনো আমাদের হয়নি। তাই নকলের মতো একটি ঘৃণ্য কাজকেও আমরা অনায়াসে সমর্থন করি, টাকার জোরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি কিনে নিই ।

Table of Contents
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : কতিপয় সমস্যা ও অসঙ্গতি
এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাচিত্র যে কতটা করুণ তা কোনো সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তুলে ধরা খুবই দুস্কর। কেননা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার নীতি, পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনাসহ সকল ক্ষেত্রে রয়েছে অসংখ্য সমস্যা আর অসঙ্গতি। এখানে বর্তমানে শিক্ষার চালচিত্র সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হলো
প্রথমত, যে কোনো জাতির শিক্ষাব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো শিশুশিক্ষা। শিশুদের যদি যথাযথ নীতি ও পদ্ধতির আলোকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে জাতি অবশ্যই লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। এক্ষেত্রে জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশের কথা প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার নীতি, পদ্ধতি, কৌশল ও ব্যবস্থাপনাসহ সকল ক্ষেত্রেই অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে।
দেশের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে শিক্ষকের অভাব, জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবন, শিক্ষকদের উদাসীনতা, পাঠ্যবইয়ের সংকটসহ অজস্র সমস্যা লেগেই আছে। আবার কিন্ডারগার্টেনের নামে দেশে যে বিপুল সংখ্যক স্কুল গজিয়েছে এগুলোর সিলেবাস, শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রভৃতি আদৌ মানসম্মত ও শিশুশিক্ষার উপযোগী কিনা তা খতিয়ে দেখার যেন কেউ নেই। তাছাড়া শহর এলাকায় যে সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গজিয়ে উঠেছে এগুলো অল্প বয়সে শিশুদের অতিমাত্রায় জ্ঞানদানের যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে তা অনেক ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হয়ে দেখা দিচ্ছে।
কেননা শিশুরা প্রথম অবস্থায় যাই শেখানো হয় তাই শেখে। তাই বলে পর্যায়ক্রমে না এগিয়ে প্রথমে যদি তাদেরকে অতিমাত্রায় চাপ দেয়া হয় তাহলে এ চাপ এক পর্যায় তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে। তখন শিশুটি শিক্ষার মূল দৌড় থেকেই ছিটকে পড়ে। তখন বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনো মাধ্যমেই সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না।
সুতরাং সমন্বিত শিশু শিক্ষানীতি না থাকায় শিশুরা ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, বিশ্বাস ও যোগ্যতায় বড় হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় ঐক্য ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশকেও বাধাগ্রস্ত করছে।
দ্বিতীয়ত, শিক্ষা একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সিলেবাস অনুযা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা হয়। এতে শিশু থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষার্থীর মননশীলতা, জাতীয় অগ্রাধিকার ও সময়ের প্রেক্ষিত বিবেচনায় সিলেবাস প্রণয়ন করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সিলেবাস প্রণয়নে আমরা এখনো ঔপনিবেশিকতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না।
আমাদের শিশুদের, বিশেষ করে ইংরেজি মাধ্যম এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুলে এখনো পশ্চিমা গল্প কাহিনী পড়ানো হয় । আমাদের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য আর বিশ্বাসের বিষয়সমূহ সেখানে খুব কম গুরুত্ব পায়। রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির দুষ্টচক্র আমাদের শিশুর মস্তিষ্ককেও নানাভাবে, বিকারগ্রস্ত করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন করা হচ্ছে।
শিক্ষার্থীদের কাছে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য আর বিশ্বাসের কোনো সমন্বিত রূপ তুলে ধরা যাচ্ছে না। ফলে এরা এক ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর অস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বড় হচ্ছে, যা জাতীয় সংহতি ও উন্নতির সমন্বিত প্রচেষ্টাকে ভণ্ডুল করার ক্ষেত্রের সূক্ষ্ম ভূমিকা পালন করছে।

তৃতীয়ত, শিক্ষার মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। একদিকে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্ক রেখে শিক্ষাদান অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে জাতিকে পরিচিত করে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার উপযোগী করে গড়ে তোলা—এ দ্বিবিধ প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এখনো এ দুয়ের মধ্যে।
সমন্বয় সাধন করতে পারিনি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নামে বাস্তবতা থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। কারণ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান সর্বত্র ইংরেজির যে রাজত্ব সেখানে আমাদের কোনো অনুপ্রবেশ নেই। তাই বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা না করে বাস্তবতার নিরিখে আমাদেরকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি গ্রহণ করতে হবে ।
ইদানীং অবশ্য ইংরেজির প্রতি বেশ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে হুট করেই নবম-দশম এবং ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে Communicative English চালু করা হয়েছে। Communicative English চালু করার আবশ্যকতা রয়েছে, কিন্তু যে শিক্ষার্থী ভালোভাবে ইংরেজি পড়তেই পারে না তার জন্য সম্পূর্ণ নতুন এ পদ্ধতির সাথে খাপ খাওয়ানো খুবই কঠিন। প্রাথমিক স্তর থেকে ক্রমে এ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রস্তুত করার সুযোগ পেত।
তাছাড়া Communicative system-এ ইংরেজি পড়ানোর আরেকটি সমস্যা হলো, ইতিপূর্বে যারা ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন তারা সকলেই ইংরেজি সাহিত্যে জোর দিতেন।
Communicative English পড়ানোর উপযোগী কোর্স আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছিল না।
যদিও ইদানীং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে নতুন কোর্স চালু হয়েছে। তাই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকরা এ বিষয়ে যথাযথভাবে পাঠদান করতে পারছেন না। অন্যদিকে সিলেবাস উপযোগী শিক্ষক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও এ দেশে নেই ।
চতুর্থত, শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি বহুলাংশে শিক্ষকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা আর আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের শিক্ষক সমাজ এক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ। এ ব্যর্থতার পেছনে অনেক কারণ থাকলেও অন্যতম কারণ শিক্ষকদের যোগ্যতার অভাব। বিশেষ করে বেসরকারি কলেজ ও স্কুলগুলোতে যে নিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে তাতে অনেক অযোগ্য লোকও ডোনেশন, স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিক প্রভাব-প্রতিপত্তির বলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছে।
অন্যদিকে একসময় শিক্ষকতা সম্মানজনক বলে বিবেচিত হলেও বর্তমানে এর প্রতি মেধাবী ছাত্রদের আগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে। শিক্ষকদের যে বেতন ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা তাতে মেধাবী লোকদের এর প্রতি আগ্রহ না থাকারই কথা। তাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ইংরেজি, গণিত ইত্যাদির শিক্ষক পাওয়া যায় না।
ইদানীংকালের আরেকটি সমস্যা হলো, ঘন ঘন সিলেবাস পরিবর্তন করে শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের চেষ্টা করা হলেও যোগ্য ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের অভাবে তা ফলপ্রসূ হয় না। এরূপ জটিলতার অন্যতম উদাহরণ হলো Communicative English চালু।
পঞ্চমত, পরীক্ষায় নকল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি দুরারোগ্য ব্যাধি। এ ব্যাধির ফলে ছাত্র- শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জাতি অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। বর্তমানের এ নাজুক অবস্থা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রের নানা অব্যবস্থাপনা আর রাজনীতির দুষ্টচক্র এ ব্যাধিকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে রূপ দিয়েছে। সার্টিফিকেটসর্বস্ব শিক্ষার প্রতি অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের দুর্বলতা মূলত নকলের ব্যাপকতার জন্য দায়ী।
পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাবও এক্ষেত্রে বিরাটভাবে দায়ী। এক্ষেত্রে সরকারকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বা রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি। তবে সম্প্রতি সরকার এ ব্যাপারে বেশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং গত কয়েকটি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সরকার সফলও হয়েছে।
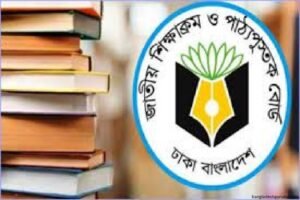
ষষ্ঠত, উচ্চ শিক্ষার প্রসারে পৃথিবী জুড়েই ইদানীং বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ ধারায় বাংলাদেশেও নব্বই দশকের শুরুতে কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে এদের সংখ্যা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বেশি। কিন্তু ইদানীং এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, টিউশন ফিসহ অন্যান্য খরচের ব্যাপকতা, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও উদ্যোক্তাদের অব্যবস্থাপনা, যোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
কেননা আমাদের মতো গরিব দেশে এ ধরনের শিক্ষার অর্থ হলো মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীকে মেধা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। তাছাড়া বিপুল অঙ্কের টাকার লোভে দিন দিন বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে কিন্তু এদের অধিকাংশেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। তাছাড়া শিক্ষা বেচাকেনার হাট থেকে উদ্যোক্তারা যে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রয়াসও চোখে পড়ে না।
সপ্তমত, প্রয়োজনীয় বই তথা পাঠ্যপুস্তকের সংকট আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর যে সকল বই বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর নিম্নমান, যথাসময়ে বিতরণ না হওয়া ইত্যাদি সমস্যা প্রতি বছরই দেখা যায়। ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শুরুই হয় তিক্ততা আর বিলম্বের মধ্য দিয়ে। তাছাড়া মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হলেও উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলায় মানসম্মত বই বেশ দুর্লভ। একদিকে বাংলা বইয়ের সংকট অন্যদিকে ইংরেজির দুর্বলতা – এ দ্বিবিধ কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অনেকক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়।
শিক্ষাব্যবস্থায় কতিপয় ইতিবাচক দিক:
অনেক অব্যবস্থাপনা, বিড়ম্বনা আর অসঙ্গতির মাঝেও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কতিপয় ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা যায়। যেমন-
১. বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় অব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় শিকার হলো আমাদের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। বর্তমানে সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উঠিয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে ৷ অবশ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে তবে বিপুল টাকার বিনিময়ে হলেও মানুষ উচ্চ শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ পাচ্ছে।
২. ইরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের রয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতা। এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও লক্ষণীয় হলো, জাতি অন্তত ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করছে। এজন্য বর্তমানে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি কিছুটা ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
৩. ইদানীং আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, মানবিকের তুলনায় বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে বাণিজ্য শিক্ষার প্রতি ঝোঁক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউটসহ প্রতিটি পর্যায়েই চোখে পড়ার মতো। সুযোগের সীমাবদ্ধতাহেতু হয়তো অনেকে কাঙ্ক্ষিত চাকরি পাচ্ছে না কিন্তু প্রায়োগিক শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অবশ্যই শিক্ষার একটি ইতিবাচক দিক।
৪. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি ইতিন চক দিক নারীশিক্ষার প্রসার। বিশেষ করে ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মেয়েদের মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দান, ছাত্রী উপবৃত্তি চালু প্রভৃতি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং এর ধারাবাহিকতায় দেশে নারীশিক্ষার হার অনেক বেড়েছে।
৫. একসময় একটি ভীতি ছিল যে, ছাত্রদের নকলের সুযোগ না দিলে পাসের হার কমে যাবে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে এবং শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হবে। কিন্তু কিছুকাল ধরে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নকল প্রবণতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে এবং পাসের হার কিছুটা কম হলেও সার্বিক শিক্ষার ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি। এমনকি ছাত্ররাও নিজেদের নকলবিহীন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে তুলছে। এ ধারা বজায় রাখতে পারলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আসবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই ।

শিক্ষার উন্নতিতে করণীয়:
শিক্ষার উন্নতি ও উন্নয়নে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে বহু শিক্ষা কমিশন গঠন হলেও প্রকৃতার্থে শিক্ষার উন্নয়ন হয়নি। তথাপি প্রচেষ্টা থেমে নেই । প্রতিটি সরকারই আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনার আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি
১. প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সিলেবাসের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন জরুরি। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে তা অত্যাবশ্যক। হঠাৎ করে এসএসসি কিংবা এইচএসসি পর্যায়ে উন্নত সিলেবাস প্রণয়ন করলেও তা ছাত্রছাত্রীরা কার্যকরভাবে গ্রহণ করতে পারছে কিনা সন্দেহ।
২. দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সমন্বয় সাধন অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে কিন্ডারগার্টেন ও মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয় সাধন জরুরি।
৩. প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ইংরেজি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া আবশ্যক। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনাকে বাধ্যমূলক করা উচিত ।
৪. পরীক্ষায় নকল বন্ধের জন্য প্রথমেই স্কুল-কলেজগুলোতে বিনা-নকলে পাস করার উপযোগী পড়াশোনা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা আবশ্যক। নতুবা নকল বন্ধ করে পাসের হার কমানো যাবে, শিক্ষার মান বাড়ানো যাবে না। আর শিক্ষার মান বাড়াতে না পারলে নকল প্রতিরোধের কোনো প্রচেষ্টাই কাজে আসবে না ।
৫. শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক। শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে না পারলে যত ভালো সিলেবাসই হোক না কেন তা ফলপ্রসূ হবে না।
৬. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য পিএসসির মতো শিক্ষক নিয়োগের একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ।
৭. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার মান নিরূপণ ও বজায় রাখার জন্য সরকারের আরো দৃঢ় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে যথেচ্ছ বেচাকেনা করার সুযোগ দেয়া অনৈতিক। এক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা পূরণের বিধান করে দেয়া যেতে পারে, যেখানে মেধাবীরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধায় পড়ার সুযোগ পাবে।

উপসংহার :
সর্বোপরি আমাদের জাতিকে শিক্ষিত করে একটি উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সচেতনতা ছাড়া কেবল পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে জাতির উন্নতি সম্ভব নয় ।